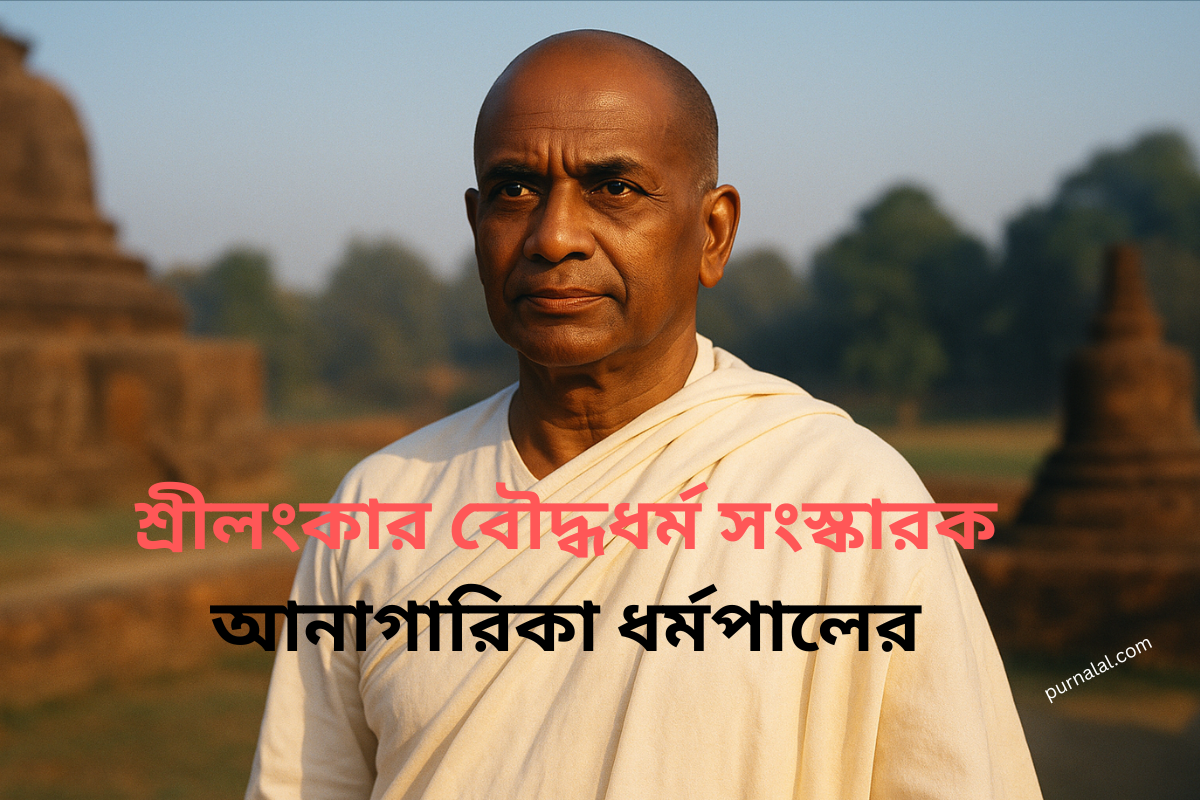আনাগারিকা ধর্মপালের নাম উচ্চারিত হলেই বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণের এক আলোকবর্তিকার কথা মনে পড়ে। শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে এমন এক সময় এসেছিল যখন বৌদ্ধধর্ম মন্দিরের ভেতরে বন্দি হয়ে পড়েছিল। ভিক্ষুরা দান-দক্ষিণার উপর নির্ভর করত, জমি ও সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করত, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন থেকে ধর্ম অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের সময় খ্রিস্টান মিশনারিরা শিক্ষা ও আধুনিকতার দায়িত্ব নিয়েছিল, আর বৌদ্ধ সমাজ পিছিয়ে পড়েছিল। ধর্ম তখন কেবল আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন।
এই অন্ধকার সময়ে আবির্ভাব ঘটে ধর্মপালের। তিনি নিজেকে প্রচলিত অর্থে ভিক্ষু বানালেন না, আবার গৃহস্থ জীবনেও রইলেন না। তিনি “আনাগারিক” বা গৃহত্যাগী পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর পোশাক ছিল সাদা, প্রতিজ্ঞা ছিল ব্রহ্মচর্যের, আর লক্ষ্য ছিল একটাই—বৌদ্ধধর্মকে আবার মানুষের জীবনে ফিরিয়ে আনা এবং শোষণ ভেঙে জাতিকে জাগ্রত করা।
ধর্মপাল বিশ্বাস করতেন, বুদ্ধের ধর্ম শুধু ভিক্ষুদের জন্য নয়, বরং সমগ্র জাতির জন্য। তাই তিনি বললেন, মন্দিরের ভিক্ষুরা যদি শুধু দান সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে, তবে তারা জাতিকে এগিয়ে নিতে পারবে না। তাদের কাজ হওয়া উচিত শিক্ষা ও সমাজসেবা।
যেমন চিন্তা তেমন কাজ। তাঁর নেতৃত্বে মন্দিরগুলো আবার প্রাণ ফিরে পেল, সেগুলো শুধু পূজা ও আচার-অনুষ্ঠানের স্থান না হয়ে স্কুল, পাঠশালা ও সমাজকেন্দ্রে পরিণত হলো। তিনি গড়ে তুললেন মহাবোধি সোসাইটি, যা শুধু শ্রীলঙ্কায় নয়, ভারত ও অন্যান্য দেশে বৌদ্ধ শিক্ষা ও পুনর্জাগরণের আন্দোলন চালালো।
শিক্ষা তাঁর সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। তিনি দেখলেন, শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধরা আধুনিক শিক্ষার অভাবে পিছিয়ে পড়ছে। ব্রিটিশরা যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল তা প্রায় পুরোটাই খ্রিস্টান মিশনারিদের হাতে। ধর্মপাল বুঝলেন, যদি বৌদ্ধরা শিক্ষিত না হয়, তবে তারা জাতি হিসেবে কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তাই তিনি স্কুল ও লাইব্রেরি গড়ে তুললেন, শিশুদের পড়াশোনার সুযোগ করে দিলেন। তাঁর এই উদ্যোগেই এক নতুন প্রজন্ম তৈরি হলো, যারা জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করল এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতার সংগ্রামে শ্রীলঙ্কার নেতৃত্ব দিল।
তবে ধর্মপাল শুধু নিজের দেশেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিনি ভারত ভ্রমণ করে গয়ার মহাবোধি মন্দির পুনরুদ্ধারের আন্দোলন চালালেন। সেই সময় এটি হিন্দু পুরোহিতদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, কিন্তু ধর্মপালের নিরলস প্রচেষ্টায় আবার বৌদ্ধদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।
শুধু তাই নয়, তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করে বক্তৃতা দিলেন। সেখানে তিনি বৌদ্ধধর্মকে আধুনিক যুক্তিবাদী ও শান্তির ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করলেন। তাঁর কণ্ঠে শোনা যেত এক দৃঢ় বার্তা—বৌদ্ধধর্ম হলো সর্বজনীন মানবধর্ম, যেখানে কুসংস্কারের স্থান নেই, আছে জ্ঞান, করুণা ও স্বাধীনতা।
ধর্মপালের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল তাঁর সংস্কারবাদী মনোভাব। তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন, ভিক্ষুরা যদি শুধু দান সংগ্রহ করে আর মানুষের বোঝা হয়ে থাকে, তবে তারা প্রকৃত ধর্মের পথে নেই। কিন্তু যদি তারা স্কুল বানায়, মানুষের মাঝে শিক্ষা ছড়ায়, সমাজের পাশে দাঁড়ায়, তবে তারাই বুদ্ধের প্রকৃত উত্তরসূরি। তাঁর আন্দোলন শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ সমাজকে নতুনভাবে আত্মবিশ্বাসী করল, তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগাল এবং জাতিকে পুনর্গঠনের পথে দাঁড় করাল।
আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে তাকালে আমরা একই বাস্তবতা দেখতে পাই। অনেক জায়গায় ভিক্ষুরা মানুষের কাছ থেকে দানের নামে অর্থ ও সম্পদ নিচ্ছে, কিন্তু জনগণের জীবন উন্নত করার জন্য কোনো কাজ করছে না। আনাগারিকা ধর্মপালের জীবন থেকে এখানেই শিক্ষা নেওয়া যায়। ধর্ম মানে শোষণ নয়, ধর্ম মানে শিক্ষা, মুক্তি এবং জাতি গঠন। ধর্ম মানে জমির মালিকানা নয়, বরং জাতির উন্নতির দায়িত্ব নেওয়া। ধর্ম মানে শুধু আচার নয়, মানুষের দুঃখ লাঘব করা।
ধর্মপাল প্রমাণ করেছেন, ধর্ম যখন সংস্কার হয় তখন তা কেবল আচার নয়, বরং জাতির পুনর্জন্ম ঘটায়। তাঁর কাজ শুধু শ্রীলঙ্কায় নয়, গোটা বৌদ্ধ বিশ্বে আলো ছড়িয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজ যদি তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নেয়, তবে ধর্ম আবার মানুষের মুক্তি ও জাতির উত্থানের শক্তি হয়ে উঠতে পারে।